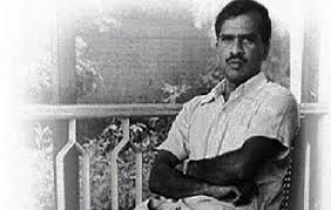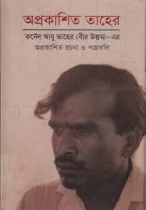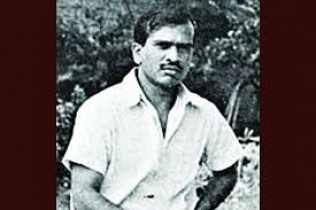জিয়ার ফাঁসির দড়ি তাঁর মাথার ওপর ঝুলছে। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাহের এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন কিছুই তাঁর হয়নি। তাঁর ফাঁসি কার্যকরই হবেনা! প্রহরীদের তাড়ায় পরিবারের সদস্যরা জেলখানা থেকে চলে এলেন।
নান্টু (তাহেরের ডাকনাম) বলে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি বা কারও কাছে যাতে তাঁর জীবন ভিক্ষা চাওয়া না হয়। কারন তিনি কোন অপরাধ করেননি। কিন্তু লুৎফারতো দরকার তাঁর স্বামী আর সংসার। তাঁর শিশু সন্তানদের পিতাকে।
এরজন্যে তাহেরের নিষেধ স্বত্ত্বেও তিনি তাঁর মতো করে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। স্বামীর জীবন রক্ষায় তখন যে যা বলেছে তার কাছে ছুটে যাচ্ছিলেন লুৎফা। পার্টির দুই সদস্য কাশেম ও শাহ আলম তখন তাঁকে বিভিন্নজনের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
একদিন তারা তাঁকে সন্তোষে মাওলানা ভাসানীর কাছে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মতো ততদিনে জিয়াকেও সমর্থন জানিয়েছেন ইতিহাসের সফেদ পাঞ্জাবির এই মাওলানা। কি ছিলেন তিনি আর কী হয়ে গেলেন!
জিয়ার পিছনে তখন যে সব রাজনৈতিক এতিম জড়ো হচ্ছিল তাদের অনেকে ছিল এই মাওলানারই লোক। মাওলানা কাউকে তাতে নাও করছিলেননা! এভাবে চোখের সামনে ভাসানী জীবিত থাকতেই তাঁর ন্যাপ দলটা শূন্য গোয়ালে পরিণত হয়ে গেল!
মাওলানা তাদেরকে নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে খেতে বললেন, তিনি সব জানেন। মৃত্যুদন্ড রহিত করার জন্যে তিনি জিয়ার কাছে তারবার্তা পাঠালেন। কিন্তু জিয়াতো তখন বেপরোয়া। ভাবখানা তার, সারাজীবনের জন্যে ক্ষমতা পেয়ে গেছেন!
অতএব মাওলানা ভাসানী বা কাউকেও তিনি তখন আর গোনায় ধরছেননা। বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন তখন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি।বিশিষ্ট নাগরিক-বুদ্ধিজীবীদের একটা দল তাঁর কাছে গেলেন।
তাঁকে তারা বললেন, প্রধান বিচারপতি হিসাবে আপনি এই অবিচার ঠেকানোর উদ্যোগ নিন। একটা নজির সৃষ্টি হোক। স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারকে এভাবে জবরদস্তিমূলক ফাঁসিতে হত্যা করতে দেবেননা।
তা ছাড়া তাহের একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। আন্তর্জাতিক আইনেও শারীরিক প্রতিবন্ধী কাউকে ফাঁসি দেয়া যায়না। কিন্তু বিচারপতিদের অনেকের তখন সামরিক শাসকদের বন্দুকের কথা মনে করলেই হাত-পা কাঁপতে শুরু করতো!
বিচারপতি আবু সাদাত সায়েম ততদিনে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহন করে জিয়ার সামরিক কর্তৃ্ত্বকেও কবুল করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন ব্যক্তিত্বহীন পা কাঁপা প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনও তখনই কাঁপতে শুরু করে দেন।
দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের সে দলটিকে মুখের ওপর না করে দেন। কোন উদ্যোগ নিতে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে বললেন, তিনি পারবেননা। তাঁর ভয় করে। বাংলাদেশে আইনের শাসন থাকলে এদের কোর্টে আনা উচিত ছিল।
আইনের শাসন রক্ষার নামে শপথ নেয়া, সামরিক শাসকদের তল্পিবাহক এসব বিচারপতিদের কোন একদিন কোন প্রজন্ম বিচার করবে। কারন তারা জনগনের টাকায় বেতন-ভাতা, অবসর ভাতা সব খেয়েছেন।
২০ জুলাই ১৯৭৬। কারাগারের বার্তাবাহক এসে কর্নেল তাহেরকে জানিয়ে গেল পরের দিন তাঁর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। তাহের সব শুনলেন। নিঃশঙ্ক চিত্তে ঠান্ডা মাথায় একটা ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলেন বার্তাবাহককে।
তাঁর এমন শীতল প্রতিক্রিয়ায় বার্তাবাহকতো অবাক! কারন সাধারনত ফাঁসির আসামীরা এমন খবর শুনে হাউমাউ করে কাঁদে। আর ইনি কিনা ঠান্ডা মাথায় বললেন, থ্যাংকু। ধন্যবাদ। চিন্তায় পড়ে যায় বার্তাবাহক! লোকটার মাথাটাথা ঠিক আছেতো!
কারাগারের নিয়ম অনুসারে একজন মৌলভী তাহেরকে তওবা পড়াতে আসেন। মৌলভী তাহেরকে বলেন জীবনে করা গুনাহ-অপরাধের কাছে আল্লাহর কাছে মাফ চান। আল্লাহ মাফ করার মালিক।
কিন্তু মৌলভীকে পাত্তাই দিলেননা তাহের। কারন তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা অকপটে বলতেন। মনে একটা মুখে একটা এমন চরিত্রের তিনি ছিলেননা। তাহের মৌলভীকে বললেন, ‘আমি নিষ্পাপ।
আপনাদের সমাজের কালিমা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কখনো না। আমি সম্পূর্ন নিষ্পাপ। আপনি এখন যান। আমি এখন ঘুমাবো’। তাঁর এমন কথায় চমকে যান মৌলভীও। কারন তাঁর কাজ হচ্ছে ফাঁসির আসামিকে তওবা পড়ানো।
কিন্তু ফাঁসির এমন আসামি এর আগে তিনি কখনো পাননি-দেখেননি। মৌলভী চলে যাবার পর জনতার তাহের সত্যি সত্যি ঘুমাতে যান। এবং ডুবে যান গভীর নিদ্রায়। যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি যুদ্ধ করেছেন সে দেশের আলো-হাওয়ায় সেটিই ছিল শেষ ঘুম, মুক্তিযুদ্ধের সাহসী বীর সেনানী তাহেরের।
২১ জুলাই ভোররাত। তিনটা। ঢাকার তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগার। ৮ নাম্বার সেল। ঘুম থেকে তাহেরকে ডেকে তোলা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে সাহায্য করতে চাইলে মৃদু স্বরে তাহের বলেন, ‘আমার নিষ্পাপ শরীরে তোমাদের স্পর্শ লাগুক, তা আমি চাইনা’।
এরপর অবিশ্বাস্য সব কাজ করতে থাকেন তাহের! তিনি দাঁত মেজে দাঁড়ি কেটে, গোসল করে নকল পা, জুতো, শার্ট-প্যান্ট নিজেই পরে নেন। তাহের জেলারকে বলেন, আমার স্ত্রী যে আমগুলো এনেছিলেন, সেগুলো নিয়ে আসুন।
জেলার আমগুলো নিয়ে এলে তাহের আম কাটেন। নিজে খান, অন্যদের খেতে দেন। চা খান এক কাপ। একটা সিগারেট ধরান। একটু পর যার ফাঁসি হবে সেই তাহেরের এমন ধীর-স্থির-শান্ত প্রকৃতি দেখে উপস্থিত কারা কর্তৃপক্ষের লোকজন প্রথমে হতভম্ব হন।
পরে মুষড়ে পড়েন। তাদের চোখের সামনে সে এক অন্য তাহের। যেন দেশপ্রেমে মোড়ানো এক জীবন্ত শরীর। অন্য কোন কথা তাঁর নেই। শুধুই দেশের কথা। সবাইকে উদ্দেশ্য করে ছিয়াত্তরের ক্ষুদিরাম বীর তাহের বলেন, ‘সবাই এত বিষণ্ন কেন?
আমি আমার দেশের দুদর্শাগ্রস্তদের মুখে হাসি উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলাম। মৃত্যু আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।’ গোপন বিচারের সময় আসামির কাঠগড়ায় তাহের যা করেছিলেন ফাঁসির আগে সে একই আচরন করেন।
ফাঁসি ঘোষনার কয়েকদিন আগে জবানবন্দী শেষে তাহের বলেছিলেন ‘আমি এ জাতির প্রানের সঙ্গে মিশে আছি। কার সাধ্য আছে আমাকে আলাদা করে! নিঃশঙ্ক চিত্তের চেয়ে জীবনে আর কোনো বড় সম্পদ নেই। আমি তার অধিকারী’।
সত্যি তাহের নিঃশঙ্ক চিত্তের অধিকারী বলেই দৃঢ় পায়ে ঠিক ভোর চারটার দিকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। নিজের হাতে জম টুপি পরেন। তাঁর শেষ কথা ছিল ‘লং লিভ মাই কান্ট্রি।বিদায় বাংলাদেশ, বিদায় দেশবাসী, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’।
মৃত্যুর আগে স্ত্রী লুৎফাকে লেখা চিঠিতে তাহের লিখেছিলেন, ‘আমাকে কেউ হত্যা করতে পারেনা। আমি আমার সমগ্র জাতির মধ্যে প্রকাশিত। আমাকে হত্যা করতে হলে সমগ্র জাতিকে হত্যা করতে হবে’।
তাহেরকে হত্যার মাধ্যমে সমগ্র জাতির মূল্যবোধকে হত্যা করেছে জিয়া। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে নিয়ে তার উল্টোপথে হাঁটার বৃত্তান্ত আজ সবাই জানে। বাংলাদেশে এখন ফ্রড মীরজাফরের ডাক নাম হয় জিয়া।
লুৎফা তাঁর স্বামীর ফাঁসির খবর পান ২১ জুলাই দিনের বেলায়। জাসদের এডভোকেট জিন্নাত আলী, কাশেম, শাহ আলম একদিন মামলার আইনজীবী প্রধান আইনজীবী আতাউর রহমান খানের কাছে লুৎফাকে নিয়ে যেতে বাসায় এলেন।
কিন্তু তখন জেলখানা থেকে ফোন এসেছে, লাশ নিয়ে যান। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন কাশেম, শাহ আলম। লুৎফাকে বললেন, ভাবী আর কোথাও যেতে হবেনা। নির্বাক বসে পড়লেন লুৎফা। কান্না ভুলে সবার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।
লাশ সরাসরি তাদের হাতে দেয়া হলোনা। তাহেরের মা-বড় ভাই সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ঢাকায় তাঁর লাশ দাফন করতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের বাদানুবাদ হয়। কিন্তু কেউ তাদের কথা শোনেনি।
একটি গাড়িতে করে তাহেরের লাশ তুলে ব্যাপক সেনা নিরাপত্তা সহ জেলগেট থেকে নেয়া হয় তেজগাঁওর হেলিপ্যাডে। আরেকটি গাড়িতে করে নেয়া হয় পরিবারের সদস্যদের। সেখান থেকে তাদের একটি হেলিকপ্টারে তোলা হয়।
হেলিকপ্টারে সামনে চাদরে মোড়ানো খাটিয়ায় শোয়ানো ছিয়াত্তরের ক্ষুদিরাম ক্র্যাচের কর্নেলের মৃতদেহ। তাঁর মাথার কিছুটা, হাঁটুর একটা অংশ চাদরের বাইরে ছিল। স্বামীর লাশ সামনে। যেন স্থির ঘুমিয়ে আছেন।
লুৎফা ভাবলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন বীরউত্তম সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে রাষ্ট্রের এ কি আচরন! হেলিকপ্টারে তিনি বা অন্য কেউ কী কেঁদেছেন? হেলিকপ্টারের শব্দে কেউ তা টের পায়নি।
নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জের এক খেলার মাঠে হেলিকপ্টার গিয়ে নামে। পরিবারের সদস্যদের বাইরে তখন শুধু মামলার অন্যতম আইনজীবী এডভোকেট জিন্নাত আলী। সে মাঠও সেখানে সেনাবাহিনীর লোকজন চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল।
গোসল-কাফনের কাপড় পড়ানোর জন্যে তাহেরের লাশ নেয়া হয় তাঁর চাচা মুনসেফ উদ্দিনের বাসায়। এই চাচা এক সময় ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। তাহেরের এই স্টেশন মাস্টার চাচাই লুৎফার সঙ্গে তাঁর বিয়ের যোগসূত্র।
বিয়ের দিন তাঁর বাসা থেকেই সেজেগুজে তাহের লুৎফাদের বাড়ির বিয়ের আসরে গিয়েছিলেন। সেই চাচার বাসাতেই লাশ হয়ে ফিরলেন মুক্তিযুদ্ধের ক্র্যাচের কর্নেল। আবার তাঁকে সেখানে সাজাতে আনা হয়েছে। এ সাজ একটি জোরপূর্বক শেষযাত্রার!
তাঁর লাশ শরীরের শেষ গোসল করিয়ে সেখানে পরানো হয় শেষযাত্রার সাজ সাদা কাফন। তাহেরের বাড়ি কাজলা থেকে শ্যামগঞ্জের চাচার বাড়ির দূ্রত্ব তিন কিঃমিঃ। লাশ শেষযাত্রার সাজে সাজিয়ে সবাই হেঁটে চললেন কাজলায়।
তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গ্রামবাসীর চাইতে সেখানে সেনা-পুলিশ সহ নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনের সংখ্যা বেশি। তারাই কবর খুঁড়লো। কবর দিলো তারাই। কবরের পাশে গড়া হলো একটি ক্যাম্প।
সেই ক্যাম্পে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন বসে-দাঁড়িয়ে পালাক্রমে পাহারা দিলো কবর। কাউকে তারা কবরের কাছে যেতে দিলোনা অনেকদিন। লুৎফা ভাবেন বোকা জিয়াউর রহমান এভাবে হয়তো ভাবলেন তাহেরকে মেরে মাটিচাপা দিয়ে দিলেন আর কী!
যেন সেখানেই তাহের শেষ! কিন্তু তাহেররা যে এভাবে শেষ হয়না, সেটি এখনও সত্য বাস্তব। ঢাকা থেকে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের অনেকে ফিরে গেলেন ঢাকায়। কাজলায় থেকে গেলেন তাহেরের বাবা-মা, লুৎফা আর আবু সাঈদের স্ত্রী।
আর সবার তাহের স্থায়ীভাবে শুয়ে থাকলেন কাজলায়। গ্রামের মাটিতে। চিরশয্যায়। চিরনিদ্রায় শায়িত থাকলেন তাহের। অন্য ভাইরা আবু ইউসুফ, সাঈদ, আনোয়ার, বেলাল জেলে। বাহার ভারতীয় হাইকমিশনের ঘটনায় গুলিতে মারা গেছেন।
কিন্তু লুৎফার তখন মনে হলো তাঁর জীবনের কোথাও কেউ নেই। একটা খা খা শূন্যতা! তাঁর আছে শুধু ছাব্বিশ বছর বয়সে সাত বছরের বৈবাহিক জীবন শেষে অকাল বৈধব্য। সন্তানদের মুখের দিকে লুৎফা তাকাতে পারেননা।
সদ্য পিতৃহারা অবুঝ তিন শিশু সন্তান আশেপাশে খেলে ঘুরে বেড়ায়। হাসে-কাঁদে। তাদের আব্বা যে আর বেঁচে নেই, সবার মতো করে কোনদিন তারা যে আর আব্বাকে আব্বা ডাকতে পারবেনা তিন শিশুর সেই বোধ হবার বয়স তখনও হয়নি।
জাসদ নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই জেলে। অন্যরা হুলিয়া মাথায় নিয়ে গ্রেফতার এড়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রায় সবাই এক রকম দিশেহারা। মুক্তিযুদ্ধের চার বছরের মধ্যে কী এলোমেলো স্বপ্ন ভাঙ্গা এক দেশ! এমন দেশের জন্যেতো কেউ যুদ্ধে যায়নি।
তাহেরের বাবা-মা’র জন্যে খুব খারাপ লাগে লুৎফার। একজন সাধারন স্টেশন মাষ্টারের স্বল্প বেতনের চাকরিতে এগার ছেলেমেয়েকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন এই বাবা-মা। তাদের সব ছেলেমেয়েই ছিল মেধাবী।
বৃদ্ধ বয়সে সব বাবা-মা একটু শান্তি-স্বস্তি চান। কিন্তু এই বাবা-মা যে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। পুরো পরিবারটি বিধবস্ত। তাহেরের মা আশরাফুন্নেসা একজন শক্ত মনের মানুষ। সবাই ভেঙ্গে পড়লেও এই মা ভেঙ্গে পড়লেননা।
সবাইকে তিনি স্বাভাবিক রাখার থাকার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। মাসখানেক কাজলায় থেকে লুৎফা চলে আসেন কিশোরগঞ্জে। বাপের বাড়িতে। ছোট মিশু এখানেই তাঁর মা তথা নানুমনির কাছে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।
মিশুকে মায়ের কাছে রেখে নিতু, যীশুকে নিয়ে ঢাকায় আসেন লুৎফা। উঠলেন তাহেরের বড়ভাই আরিফ ভাইজানের বাসায়। কারন এই অবস্থায় তিনটি শিশু বাচ্চাকে সামলানো, ভরনপোষনের ব্যবস্থা করা লুৎফার কাছে দুরুহ মনে হয়।
বাচ্চাদের বাঁচাতে মানুষ করতে তাঁর এখন একটা চাকরি বা কিছু একটা করা দরকার। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে তখন ফিল্ড অফিসার নেয়া হচ্ছিল। বারডেমের ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের পরামর্শে ওই পদের জন্যে আবেদন করলেন।
তাঁর চিকিৎসক বাবা’র বন্ধু এই ডাঃ ইব্রাহিম। অকাল বিধবা মেয়েটির পাশে দাঁড়ানোকে তিনি তাঁর দায়িত্ব মনে করেছেন। লুৎফা কিছু এনজিওতেও আবেদন করলেন চাকরির। যে যে অপশন বলছিল তাই চেষ্টা করছিলেন লুৎফা।
একদিন জেনারেল মঞ্জুর তাঁকে তাঁর বাসায় যেতে অনুরোধ করলেন। তাহেরের সঙ্গে মঞ্জুরও একাত্তরে পাকিস্তান থেকে সপরিবারে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আরিফ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে একদিন লুৎফা গেলেন মঞ্জুরের বাসায়।
লুৎফাকে সেখানে কিছু প্রস্তাব দেয়া হয়। যেমন লুৎফা চাইলে তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে। চাকরি দেয়া হবে কোন একটি বিদেশি দূতাবাসে। এমন প্রস্তাব গ্রহন করলে লুৎফা বাচ্চাদের নিয়ে ভালো থাকবেন।
লুৎফা বুঝতে পারেন এমন প্রস্তাবের নেপথ্যে বিশ্বাসঘাতক জিয়ার ভূমিকা আছে। মনে মনে ভাবেন তাহেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েও জিয়ার বদমাইশি থামলোনা! এখন লুৎফাকে কিছু একটা দিয়ে তাঁকে লোভী হিসাবে প্রচার করাতে চাইছে!
যেমন তাহেরকে গ্রেফতারের পর মুক্তিযুদ্ধকালীন জেড ফোর্সের চিকিৎসক মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ হাই’র মাধ্যমে তাঁকে কিছু টাকা পাঠানো হয়েছিল। ডাঃ হাই একজন সজ্জন মানুষ। তাঁর পরিবারও মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে তুরা ক্যাম্পে ছিলেন।
কিন্তু লুৎফা ওই টাকা স্পর্শ করেননি। টাকা নিয়ে আসা বাহকের মাধ্যমে তখনই বিশ্বাসঘাতক জিয়ার টাকা ফেরত দেন। এবার ফেরত দিলেন জেনারেল মঞ্জুরের প্রস্তাব। কিছুদিনের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের চাকরিটা হয়ে গেলো।
মোহাম্মদপুরের আজ রোডের একটি প্রায় পরিত্যক্ত বাড়ির বরাদ্দ পেলেন মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে। জেলে থাকা আবু ইউসুফের পরিবারও সে বাড়িতে উঠলো। এভাবে নতুন করে পাতা সাজানো এক হযবরল সংসারের পথ চলা শুরু হয়।
তাহের কোন সম্পদ বা ব্যাংকে কোন টাকা-পয়সাও রেখে যাননি। অনেক কষ্ট নিয়ে গেছেন। অনেক কষ্ট রেখে গেছেন। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দ্বিতীয় গ্রেডের চাকরির বেতন আর চরম আর্থিক সংকটই থাকে সর্বক্ষনিক সঙ্গী।
এরমাঝে ১৯৭৭ সালে মারা যান লুৎফার বাবা। মনে হচ্ছিল মাথা ওপর থেকে যেন বাকি ছাদটাও সরে গেলো। এরপরও কারও কাছ থেকে কোন আর্থিক বা কোন রকমের সাহায্য নেবেননা এটিই ছিল তাঁর দৃঢ়তা।
ছেলেমেয়েদের কাছের একটা স্কুলে দিয়ে প্রতিদিন অফিসে যেতেন লুৎফা। নিয়মিত বাজার-রান্না করা, পার্টির লোকজনের খোঁজ রাখা সবই চলতে থাকে এক সঙ্গে। বছর পাঁচেক পর তাহেরের ভাইয়েরা আস্তে আস্তে জেল থেকে বেরুতে শুরু করেন।
এরপর থেকে পরিবার ও দলের ভিতর থেকে তাঁর প্রতি মানসিক সমর্থন বাড়তে থাকে। লুৎফা বুঝতে পারেন এরাই তাঁর আপনজন। এরাই তুলে ধরবে তাহেরের আদর্শের পতাকা। এদের দ্রোহে নিঃশ্বাসে সৃষ্টিতে বেঁচে থাকবেন বীর তাহের।
আজ জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে লুৎফা দেখেন তাহেরের সাথীরাই তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তারাই তাহেরকে নিয়ে ভাবেন, তাঁকে নিয়ে গবেষনা করেন বই লিখেন। নাটক মঞ্চস্থ করেন। ২০১৪ সালে তাঁকে বিশেষ একটি সম্মান দেয় দল।
দলের মনোনয়নে তাঁকে সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য করা হয়। বাংলাদেশে এমপি মানেইতো সরকারি প্লট সহ নানাকিছু! কিন্তু এসবের কিছুই নিলেননা লুৎফা। তাহেরের মতো কোন লোভ লুৎফাকেও স্পর্শ করতে পারেনি।
১৯৭৪ সালে তাহেররা যখন নারায়নগঞ্জে থাকতেন তখন এত তরুন বিদেশি সাংবাদিক তাদের বাসায় আসেন। তাহের লুৎফাকে পরিচয় করিয়ে দেন ইনি লরেন্স লিফশুলজ। এক মার্কিন সাংবাদিক। বাংলাদেশের নদী ও বন্যা সামাল দেয়া নিয়ে জানতে আগ্রহী।
তাই সে এ নিয়ে তাহেরের ভাবনা জানতে এসেছিল। সেই বিদেশি সাংবাদিক ল্যারি আজ দেশে বিদেশে তাহের গবেষনারও অন্যতম চরিত্র এই লিফশুলজ অথবা ল্যারি। এ নিয়ে তাঁর একাধিক বই এরমাঝে বেরিয়েছে। আরেকটি বই প্রকাশনার পর্যায়ে আছে।
ঢাকার জেলগেটে যখন তাহেরের বিচার শুরু হয় তখন থেকে ল্যারি লিখছেন। এর সচিত্র খবর বিদেশের পত্রিকায় ছেপে হৈচৈ ফেলে দেন এই মার্কিন সাংবাদিক। জিয়ার পুলিশ-সেনাবাহিনী তাঁকে ধরে বিমানে তুলে দিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করে।
এতে করে জিয়ার নৃশংস স্বরূপ আর ল্যারির বই’র প্রচার বেশি হয়। হাঁটু বুদ্ধির জিয়ার অবশ্য বুঝতে দেরি হয়েছে ‘কী করিলে বিপদ অথবা উপকার বেশি হয়’। ল্যারির বই ‘তাহের’স লাস্ট ট্রিটমেন্ট’ পড়ে এই প্রহসনের বিচার সম্পর্কে জানে বিশ্ব।
জিয়া যুগে বইটি ও ল্যারিকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়। তাহেরের বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচারের বিরুদ্ধে তাহের পরিবার এবং জাসদ নেতৃবৃন্দ ২০১১ সালে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন। লরেন্সকেও তখন আদালতে ডাকা হয়।
আমেরিকা থেকে লরেন্স ঢাকা এসে আদালতে তাঁর বক্তব্য দেন। দৈনিক ইত্তেফাক তখন তাঁর বক্তব্যের শিরোনাম করে ‘কর্নেল তাহেরকে বিচারের নামে হত্যা করা হয়েছে’। আদালতকে ল্যারি বলেন, জিয়া মনে করতেন তাহের তাঁর পথের কাঁটা।
এরজন্যে তথাকথিত বিচারের নামে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এই সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহের বীরউত্তমকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তথাকথিত বিচারের নামে জিয়া তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলান। এটা বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য।
তাহের হত্যায় ‘একজন জড়িত থাকলে তিনি জিয়া’। তখন ল্যারির আদালতের বক্তব্য নিয়ে এই শিরোনাম করে প্রথম আলো। পত্রিকাটির রিপোর্টে আরও বলা হয়, আদালতকে লরেন্স বলেছেন, ‘গোপন বিচারে লে কর্নেল এম এ তাহেরের মৃত্যুদন্ড একটি হত্যাকান্ড’।
তাহেরকে হত্যার দীর্ঘ ৩৩ বছর পর বাংলাদেশের হাইকোর্ট তাহেরের প্রহসনমূলক বিচারের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক রায় দেয়। বিচারপতি এ এইচ এম শাসুদ্দিন চৌধুরী, বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনের বেঞ্চ বিচার শেষে দেন এই রায়।
রায়ে তাহেরকে দেশপ্রেমিক আর জিয়াকে ঠান্ডামাথার খুনি আখ্যা দেয়া হয়। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের রায় তাঁকে আবার প্রকৃত দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়ে তাঁর সব মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় এটি সম্ভব হয়েছে। এর আগে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা পদক দেন। কিন্তু তাহের হত্যারক জিয়ার স্ত্রীর হাত থেকে তখন শহীদ তাহেরের পরিবার পদক গ্রহন করেননি।
১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তাহেরের পদক পরিবারকে দিতে চান তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মাহবুবুর রহমান। কিন্তু তাহেরের পরিবারের পক্ষে বলা তারা শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে থেকেই এই পদক গ্রহনে রাজি।
এরপর গণভবনে অনুষ্ঠান করে তাহেরের মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা পদক সব তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর পদক দেয়া হয় বীরমাতা আশরাফুন্নেসার হাতে। এভাবে হত্যার কুড়ি বছর বীরউত্তম তাহেরের সম্মাননার প্রতীক পরিবারের হাতে আসে।
বাংলাদেশের আইনে মৃত ব্যক্তির বিচারের বিধান নেই। নতুবা আজ তাহের হত্যার দায়ে জিয়াউর রহমানের মরোত্তর বিচার হতো। সর্বশেষ উচ্চ আদালতের রায়ের পর তাহেরকে অবমাননার মুখ নেই বিএনপির।
কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের কিছু স্বজন মাঝে মাঝে ঘাতক জিয়ার সৈনিকদের ভূমিকা নেন! এরা প্রায় এই বীর মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র হননের চেষ্টা করেন! তারা খন্ডিত তাহেরকে দেখেন।
কারন তাঁর বিপ্লবের স্বপ্ন তখন সফল হয়নি। তাঁর ভুলও ছিল। ভুলের বাইরে বা উর্ধে আমরা কেউ নই। তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপট সীমাবদ্ধতা যারা বিবেচনায় না রেখে তাঁর ব্যাপারে এলোমেলো মন্তব্য করেন, এটা তাদের সীমাবদ্ধতা।
তাহের রোমান্টিক বিপ্লবী ছিলেন? হ্যাঁ, পৃথিবীর সব বিপ্লবীরাই রোমান্টিক ছিলেন। রোমান্টিক না হলে ভালো বিপ্লবী হওয়া যায়না। ভালো ধান্ধাবাজ হওয়া যায়। রোমান্টিক হওয়াটা একজন বিপ্লবীর আবশ্যিক যোগ্যতা।
পচাত্তরের বিশ্বাসঘাতক প্রতারক জিয়ার পাপ-তাপ ধারন করে যীশুর মতো প্রান দিয়েছেন ছিয়াত্তরের ক্ষুদিরাম তাহের। নিঃশঙ্ক চিত্ত এই মহান মুক্তিযোদ্ধাকে কেউ ছোট করতে চাইলে তাতে তিনি ছোট হন না। ছোট হয় বাংলাদেশ। ছোট হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন। ক্ষতি হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ঐক্যের।